একাডেমিতে যে কয়টা ভড়ং অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, তার মধ্যে অন্যতম হলো ‘এথিকস’। একাডেমির এথিকস হলো অনেকটা বাংলাদেশে খাদ্যপণ্যের গায়ে গুণমানের স্টিকারটার মতো। ওটা থাকা প্রায় আবশ্যিক। ভিতরের বস্তুটার গুণমান ততোটা আবশ্যিক নয়। মানে আপনি যদি মোটামুটি ভুষির উপরেও সুজির বিজ্ঞাপন আর একটা গুণমানের স্টিকার লাগাতে পারেন, তাহলেই আপনি গুণমানে পাশ।
একাডেমির এথিকস এর কাছাকাছিই একটা জিনিস। তো, সেখানে লোকজনের নাম গোপন রাখার সেমি-আইনী বিধান আছে। পাশ্চাত্যে এসব পালন না-করলে চাকরি চলে যেতে পারে। এখানে এখনও সেই সম্ভাবনা কম। তাছাড়া এর মধ্যে ‘অটোএথনোগ্রাফি’ বলে নতুন এক ফান্ডা চালু হওয়াতে এথিক্সের প্রহরীরা ঠিক কোন দিক দিয়ে তলোয়ার চালাবেন তা বুঝে উঠতে সময় নিতে থাকছেন; সম্ভবত।
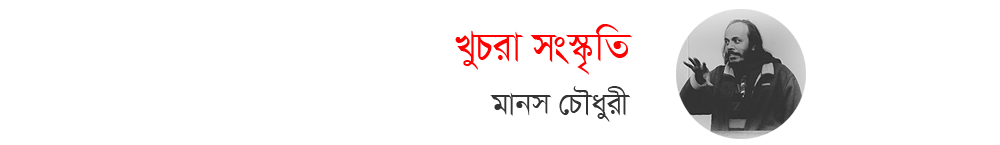
তো সেই সকালে আমার নাস্তা খাবার স্থানটি হলো গিয়ে জনসন রোড। সামাজিক বিদ্যার লোক গ্রামের নাম বদলে-টদলে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে এথিক্যাল থেকেছেন। সেই হিসাবে রাস্তার নামটাও নাহয় বদলে বেনসন রোড বানাতে পারতাম। বানানো হয়নি আরকি! কিন্তু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারটি যাতে কিছুতেই আপনারা বুঝতে না পারেন সেজন্য প্রতাপপুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার রাখা হলো। এথিক্যাল প্র্যাক্টিস! এই মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের নাস্তার একটা সামাজিক প্রশংসা ঢাকা (ঢাকার নাম কি নেয়া যাবে!) শহরে বিরাজমান আছে। আর এদের অনেকগুলো শাখা আছে।
তো জনসন রোডে পৌঁছে আমার হাতে সময় আছে। সামনে প্রতাপপুর দোকানে পরাটা-হালুয়া-নিরামিষ সব্জির গন্ধ নাকে উস্কানি দিচ্ছে। আমার বাধা কেবল নাস্তা-পরবর্তী সম্ভাব্য শারীরবৃত্তীয় চ্যালেঞ্জ। এই রোডের নাম জনসন বা বেনসন যাই রাখেন না কেন, দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণরক্ষীদের কাছে হাত-পা ছেড়ে সাহায্য চাওয়া ছাড়া কোনো পথ দেখি না। দুয়েক মিনিট পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও লাভ বিবেচনা করে, প্রতাপপুরের দারুণ নাস্তা বাদ দেয়া অসম্ভব মনে হলো। রিসার্চে এগুলো করতে হয়। রিস্ক-এসেসমেন্ট!
কিন্তু ‘মজনু’র নাম মজনু না-রাখলে তো এই বিবরণীই নিরর্থক হয়ে যায়। আমি নামটা বদলে যদি ফরহাদ বা চণ্ডীদাস দিতামও, তাতে অবধারিতভাবে তিনি ম্লান হয়ে যেতেন। তাহলে এখানে এথিক্স রাখতে গিয়ে তাঁকে ম্লান করার অঘটন আমি কেন ঘটাব? আমি মজনুকে বললাম, “আপনি তো একাই ৩ জনের কাজ করতে থাকেন দেখছি।”
তিনি বললেন, “আমি ২৫ বছর ধরে এই দোকানেই আছি।”
এইখানে আমি আসলে ৩৫ শুনেছিলাম। ভুলেই হবে। কারণ এরপরের হিসাব মানতে গেলে তিনি ৫ বছর বয়স থেকে খাবার-দাতা/‘ওয়েটার’ ছিলেন বলে মানতে হবে। কিন্তু ৭/৮ বছরের ওয়েটার ইহজনমে আমি অনেক দেখেছি। তাহলে ৩৫ বছরও তিনি বলতে পারেন। ৪০/৪৩ এর কী এমন পার্থক্য। যাহোক, কিছু প্যাঁচ এক-রাউন্ড রিসার্চে থাকতেই পারে।
চাঁদে এতবার রকেট, মানুষ, কুকুর আরও কী কী পাঠিয়েও বিতর্কনিষ্পত্তি হচ্ছে না! ৩৫ বছর হোক বা ২৫ বছর, এই প্রতাপপুরে তিনি বহাল আছেন—এটা শুনেও পুরোটা বোঝা যায় না। মানে তিনি কি প্রতাপপুরের অন্যান্য শাখাতে ছিলেন? তিনি কি এই শাখাতেই ৩৫/২৫ বছর ধরে আছেন? এই বিল্ডিংটি কি তাহলে অন্তত ৩৫ বছরের পুরানো? তাহলে রেনোভেশনটি কবে হলো (মানে এই প্রতাপপুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ইন্টেরিয়র অবশ্যই নতুনতর)? এসব প্রশ্ন মাথায় রাখার সুযোগ কম ছিল। সামনের রেকাবিতে তিনভাগে তরকারি—হালুয়া, অপেঁয়াজ ফোঁড়নদার ছোলার ডাল এবং ফোঁড়নদার সব্জি—ও পরাটা এসে হাজির। এখানে ডিফল্ট পরাটা হলো তেলহীন, আর সেটাই আমার পছন্দ। ফলে আলাদা করে বলতে হলো না।
মজনু, যাঁর নাম তখনও জানি না, ধুম করে জানালেন, সাড়ে তিনশো টাকা। ধুম করে হতেই হবে। ওই যে একজনে তিনজনের কাজ করতে-থাকা লোক তিনি। এই টেবিল থেকে ওই টেবিল। যাই করবেন ধুম করেই হবে। তার মধ্যে একটা সংলাপ চলছে আমার সাথে। এই সাড়ে তিনশো’র ঠিকানা অবশ্য ওই ক্ষুধা লোভের মধ্যেও আমি ভুল করিনি। অনেক নিরীহ গবেষক কোনোকিছুই আগাম ধরে নিতে চান না। এটা নাকি তাঁদের ‘পদ্ধতি’! তাঁরা যদি পদ্ধতির স্বার্থে এরপর প্রশ্ন করতেন যে “মাসে?”, তাহলে আপনি তাঁদের আক্কেল ধরে গালি দিতে পারতেন, কিন্তু গবেষণা পদ্ধতিতে দোষ দিতে পারতেন না। যাহোক, আমি দিনে সাড়ে তিনশো’র এই হিসাবে একটু ভিড়মি খেলাম। মৃদু! মানে বাংলাদেশে বাস পর্যন্ত চলছে দৈনিক-সাবলেটে; রেঁস্তোরা তো চলবারই কথা। কিন্তু প্রতাপপুরের মতো পুরানো প্রতিষ্ঠানে এই “আসিলে পয়সা পাইবে” নীতিটাতে ছোলার ডাল কিছুটা বিস্বাদ লাগল। তবে মজনুর নাম তখন আমি জিজ্ঞাসা করে ফেলেছি—”নাম কী আপনার?” ততক্ষণ পর্যন্ত নামহীন মহাতৎপর ওয়েটার জানালেন— “মজনু! আর পাইবেন না। ৪০ বছর আগের নাম।” আমি বললাম—”বটেই, নামটা তো ৪০ বছর আগেই রাখা!” তিনি বললেন—”হ! এখন এই নাম কে রাখব?”
মজনুর মুখে দাড়ি। আমার মুখে মৃদু দাড়ি। দেখি ম্যানেজারের মুখেও স্পষ্ট দাড়ি। ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের দাড়ির মতো স্টাইল কমবেশি। আমারটাই স্টাইলহীন। আমার সামনে এক দাড়িহীন ঝাড়িবাজ লোক এসে বসলেন। মুরুব্বি। এসেই এমন জোরালো গলায় হৈচৈ করে পানি চাইলেন যে আমি খাওয়া বাদ দিয়ে তাঁর গলা নিয়ে কিছু বলার প্রস্তুতি নিলাম। তিনি পানিও চাইলেন এক মিনিটেই তিনবার। প্রতিবারই আগেরবারের তুলনায় কর্কশ ও জোরালো। ‘তুই’ তাঁর ডিফল্ট সম্বোধন। আমাকে অবশ্য ডাকেননি। মজনুবৃন্দকেই ডাকাডাকি করেছেন।
আমি যখন প্রায় নিশ্চিত যে তাঁর এই বাজখাঁই গলায় তটস্থ করা নিয়ে কিছু বলব, তখন তিনি একটা ডাব্বা বের করলেন ব্যাগ থেকে। আমি ভেবেছিলাম বলব যে “এত হৈচৈ করলে আমার খাবার হজম হয় না।” কিন্তু দেখি ডাব্বাভর্তি ওষুধ। তারপর তিনি ইনসুলিন ইনজেক্ট করলেন। ততক্ষণে খাবার চলে এসেছে। তিনি হুমহাম করে খেয়ে একটা সিকিহাসি দিয়ে উঠে বিল দিতে চলে গেলেন ম্যানেজারের ডেস্কে। ভাগ্যিস কিছু বলিনি। ইনসুলিনগ্রহীতা নাস্তা খেতে এসে যেকোনো আওয়াজেই কথা বলতে পারেন বলে রায় দিয়ে আমি আমার সময়ক্ষেপণের নাস্তা করতে লাগলাম।
ম্যানেজারের পিছনে দুইখানা ছবি টাঙানো। এই এক যন্ত্রণা! দোকানে কারও ছবি টাঙানো থাকলে সেই লোকগুলোকে জীবিত ভাবা এত কঠিন! কেবল ফোটো স্টুডিওই এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মানা যেতে পারে, যদি দুচারটা ফোটো স্টুডিও এখনও আপনারা খুঁজে পেতে ছবি তুলতে যান। আসলে চুল-কাটার দোকানেও মানা যেতে পারে। অন্যান্য দোকানে কারো ফ্রেমবাঁধা ছবি টাঙানো থাকলে তাঁদের জীবিত ভাবার কোনো চেষ্টাই আমার মাথা কখনো মানতে রাজি থাকেনি! আবার “ওনারা কি বেঁচে আছেন?” এই প্রশ্ন করার মতো ধৃষ্টতা বা অর্বাচীনতাও দেখানো কঠিন। সবটাই কঠিন। যদি এলাকার এমপির ছবি থাকার বিধান থাকত, তাহলে আমার মাথার এই সমস্যাটা দেখা দিত না। জানা মতে, এখনও রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপনে কেবল দুইজনের ছবি টাঙাতেই বলা আছে, এমপিদেরটা এখনও আসেনি।
সত্যি বলতে, এমনকি মেয়রও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্রীয় বিধানের সেই দুজন এই দুজন নন। তাহলে তো আলাপই উঠত না। আমি দুটো ছবিই আমার চেয়ার থেকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি। আমি এখনও মাইনাস চশমা নিই না। বাইফোকালের ঝামেলা এড়ানোর জন্য। খুব অসুবিধাও হয়নি। আমি থুতনি, চুল, কান ইত্যাদি দেখে এক লোকের দুই কালের ছবি হিসাবে রায় দেবার কয়েকবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খুব একটা কনভিন্সিং লাগল না। দুইজনই। অবশ্যই। কিন্তু এক দোকানে দুইজন কাছাকাছি বয়সের ‘মৃত’ মানুষ! নিষ্ঠুরতা ছাড়াও এর লজিক্যাল দিক গোলমাল হয়ে গেল পুরা।
জীবিত না মৃত তা বুঝবার আরেকটা বিরাট সুযোগ থাকে। সেটা সাধারণত ফুলেরা দিয়ে থাকে। ফুলের মালা যদি ছবির ফ্রেমে পরানো থাকে, তাহলে আপনি ১০০ ভাগ মৃত মানুষ ধরে নিতে পারেন। কিন্তু, ফুলের মালা নেই বলে ১০০ ভাগ জীবিত তাঁরা তা কিছুতেই ধরে নিতে পারবেন না। কিন্তু ঝামেলাটা অন্যত্র।
এই প্রতাপপুরের মালিক যদি হিন্দু না হবেন, তাহলে মৃত মানুষের ছবিফ্রেমে ফুলের মালা কীভাবে দেবেন? কেন দেবেন? জনসন বা বেনসন রোডে ফুলের দোকানই বা কই? থাকলেও কি তাঁরা আর দিতেন? তাছাড়া প্রতাপুরের শয়ে শয়ে শাখার একই মালিক তা ভাবার মতো বিদঘুটে চিন্তাই বা কীভাবে প্রশ্রয় দেবেন? আর যেহেতু ব্রান্ডটি ‘জনপ্রিয়’, তাহলে কোনো শাখার অহিন্দু মালিক কি থাকবেন না? কিন্তু হিন্দু মালিকই কি মৃত লোক পেলেই ছবিতে আর আরাম করে ফুল দেবেন? সুলভে মাগনা পেলেও কি দেবেন? যদি না দেন তাহলে কি ফুলের প্রতি বিরাগ হিসাবে দেখবেন? নাকি সামাজিক সতর্কতা হিসাবে দেখবেন? নাকি কী কী যে করবেন, সব প্যাঁচ লাগিয়ে আমার নাস্তা শেষ হলো। আমি বিল দিয়েছিলাম টেবিলে বসে।
মজনু বললেন, “ম্যানেজাররে কইয়েন।” আমি ওই কয়েক সেকেন্ডে কিছুতেই বুঝতে পারলাম না যে কী ‘কইতে’ হবে—বিল দিয়েছি, নাকি মজনু তৎপর কর্মী, নাকি সাড়ে তিনশ অতি মন্দ মজুরি, নাকি বেতনটাকে মাসিক করার অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক মজুরি ব্যবস্থা কায়েম করতে। দোকান থেকে বের হয়েই কেবল সিদ্ধান্ত নিলাম, প্রথমটাই হবে।
পড়ুন: খুচরা সংস্কৃতি’র আরো লেখা
ম্যানেজারের ডেস্কে প্রায় খামোকা দাঁড়ালাম। আমার চশমাটা বুকে, প্রায় ভুলে গেছি। আমি চোখ সরু করে সরকারপ্রদত্ত খাদ্যদোকান সনদটা পড়ার চেষ্টা করলাম। অনেক কসরতে শেষ বাক্যে পড়তে পারলাম—”অমুক রাণী ঘোষের নামে দোকানটি…” ইত্যাদি।
মাথায় অনেক সাজিয়ে ম্যানেজারকে প্রশ্ন করলাম, “ওনারা কি দুইজন?”
ম্যানেজার বললেন—”শালা দুলাভাই।”
আদাবর, ঢাকা, ৩ নভেম্বর ২০২৩
(ঘটনকাল: ১ নভেম্বর ২০২৩)




